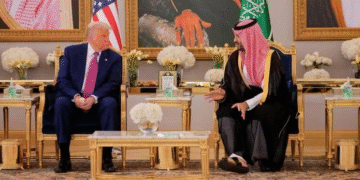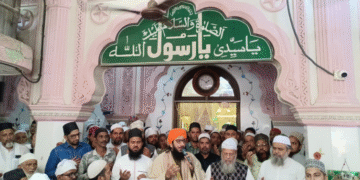বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) দেশের ইন্টারনেট জগতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সরবরাহকারীদের, বিশেষত এলন মাস্কের স্টারলিংক, বাংলাদেশি বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করতে নতুন এক নীতিমালা খসড়া করা হয়েছে।
“বাংলাদেশে নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (এনজিএসও) স্যাটেলাইট পরিষেবা পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রক ও লাইসেন্সিং নির্দেশিকা” নামের এই নীতিমালায় শতভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) সুযোগ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
একনজরেঃ
১. বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো এনজিএসও স্যাটেলাইট পরিষেবা পরিচালনা করতে পারবে।
২. শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
৩. পাঁচ বছরের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হবে।
৪. ব্রডব্যান্ড, আইওটি ও ইন্ট্রানেট সেবা প্রদান করা যাবে।
৫. আবেদন ফি ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ।
৬. অধিগ্রহণ ফি $১০,০০০ এবং বার্ষিক ফি $৫০,০০০।
৭. দেশের মধ্যে গেটওয়ে সিস্টেম স্থাপন বাধ্যতামূলক।
৮. ট্রাফিক যাচাই ও রাউটিং স্থানীয় গেটওয়েতে হবে।
৯. এফডিআই নীতি ও বিডা নীতিমালা মানতে হবে।
১০. স্থানীয় ডেটা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে গেটওয়ে স্থাপন।
নতুন নির্দেশিকার অধীনে, বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে এনজিএসও স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ও পরিষেবা “নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা” করতে পারবে। তবে এদের বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্ধারিত এফডিআই নীতিমালা মেনে চলতে হবে।
বিটিআরসি সম্ভাব্য অপারেটরদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো নির্ধারণ করেছে। লাইসেন্সের মেয়াদ পাঁচ বছর, এবং অপারেটররা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট পরিষেবা, আইওটি, এবং মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগের মতো সেবা প্রদান করতে পারবে। আর্থিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকছে ৫ লাখ টাকা আবেদন ফি, $১০,০০০ অধিগ্রহণ ফি এবং $৫০,০০০ বার্ষিক ফি।
স্থানীয় অংশগ্রহণ ও ডেটা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে নির্দেশিকায় অপারেটরদের জন্য বাংলাদেশে অন্তত একটি গেটওয়ে সিস্টেম স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই স্থানীয় গেটওয়ে দেশের মধ্যে ব্যবহারকারীর সব ট্রাফিক যাচাই ও রাউট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
টেলিকম নীতি বিশ্লেষক মুস্তাফা মাহমুদ হুসাইন বলেছেন, “এনজিএসও স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শীঘ্রই একটি রূপান্তরমূলক পরিবর্তন দেখতে পাবে।” তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন, এবং ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।
তবে চ্যালেঞ্জগুলোও বিদ্যমান, বিশেষ করে খরচের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, স্টারলিংক সেবার মাসিক চার্জ প্রায় $১২০, যেখানে প্রাথমিক হার্ডওয়্যার খরচ $৩৫০ থেকে $৫৯৯ পর্যন্ত। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় ইন্টারনেট সেবাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি, যারা সাধারণত ৫ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রায় ৫০০ টাকায় অফার করে থাকে।
বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি জায়ান্টরা স্যাটেলাইট ইন্টারনেট বাজারে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় রয়েছে। স্পেসএক্সের স্টারলিংক ইতোমধ্যে ৬০টিরও বেশি দেশে ৪,৫১৯টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করছে। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়ানওয়েব এবং অ্যামাজনের প্রজেক্ট কুইপার।
বাংলাদেশ যখন এই বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছে, তখন দেশটি একটি সম্ভাব্য ইন্টারনেট বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করবে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষার ওপর।