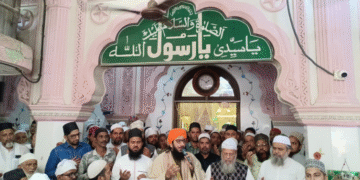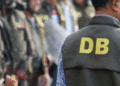অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে স্বার্থের লড়াই নাকি ‘বিপ্লবের চেতনার’ বিশ্বাসঘাতকতা?
বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে নতুন এক বিতর্ক— “সেফ এক্সিট” ইস্যু। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত এই প্রসঙ্গ আরও জটিল ও উত্তপ্ত করে তুলেছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের।
একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, সরকারের কিছু উপদেষ্টা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষায় সরকারের নীতি ও ‘বিপ্লবের স্পিরিট’-এর সঙ্গে বেইমানি করেছেন। এমনকি তিনি সরাসরি একজন উপদেষ্টার নামও উল্লেখ করেছেন, যা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
জুলকারনাইন সায়ের বলেন,
“নাহিদ ইসলাম সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন এবং অনেকে ‘সেফ এক্সিট’-এর চিন্তা করছেন। আমি মনে করি নাহিদ ভুল বলেননি। আমি নিজেও এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যা প্রমাণ করে, কিছু উপদেষ্টা প্রকৃত পরিবর্তনের চেতনার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।”
তার এই মন্তব্যের পর থেকেই অন্তর্বর্তী সরকারের নীতি-আদর্শ, নৈতিকতা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
সায়ের তার বক্তব্যে এক উপদেষ্টার পরিবারের আর্থিক লেনদেনের বিষয়ও তুলে ধরেন। তার দাবি, ২০২১ সালে সাবেক ব্যবসায়ী নসরুল আহমেদ বিপু পরিবারের মালিকানাধীন “হামিদ সোয়েটারস” নামের একটি বৃহৎ পোশাক কারখানা উপদেষ্টার স্বামী আবু বকর সিদ্দিকী ও তাদের ছেলের নামে হস্তান্তর করা হয়।
“৬০০ শ্রমিকের বিশাল এই কারখানার সম্পদমূল্য কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা,”
বলেন সায়ের।
তিনি আরও যোগ করেন,
“আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই হস্তান্তরের কোনো বৈধ নথি বা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বরং একাধিক সূত্র বলছে, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগে বিষয়টি গোপনে সম্পন্ন হয়।”
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন,
“এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেন এই ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পদে আনা হলো? এটি কি রাজনৈতিক যোগ্যতার কারণে, নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য?”
‘সেফ এক্সিট’ শব্দগুচ্ছটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিধানে নতুন নয়। অতীতে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন কিংবা ২০০৭ সালের সেনা-সমর্থিত সরকারের সময়েও এ শব্দটি শোনা গিয়েছিল।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি ইঙ্গিত দিচ্ছে— কিছু উপদেষ্টা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাচ্ছেন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন,
“সেফ এক্সিট মানে হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কেউ রাজনৈতিক দায় এড়িয়ে নিরাপদে অবস্থান নিতে চান—চাই সেটা বিদেশে হোক বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আড়ালে।”
সায়েরের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে—
অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে কি স্বার্থের সংঘাত ও বিভাজন তৈরি হয়েছে?
একজন প্রাক্তন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন,
“অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য ছিল দুর্নীতিমুক্ত শাসন, স্বচ্ছতা ও গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কিন্তু এখন যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা গোপন লেনদেন সামনে আসে, তাহলে সরকার নিজের নৈতিক অবস্থান হারাবে।”
সায়েরের অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার পরও সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি।
অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা নিজেও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।
এই নীরবতা রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে বিতর্ক—
“যদি অভিযোগ মিথ্যা হয়, তবে সরকার কেন ব্যাখ্যা দিচ্ছে না?”
একজন তরুণ রাজনৈতিক কর্মী লিখেছেন,
“আমরা ভেবেছিলাম এই সরকার পরিবর্তনের প্রতীক হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কিছু মানুষ ক্ষমতার নতুন পোশাকে পুরনো খেলা খেলছে।”
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. মাহবুব হাসান মনে করেন,
“সেফ এক্সিট মানে কেবল পদত্যাগ নয়। এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যেখানে ব্যক্তি বুঝতে পারেন—ব্যবস্থা বদলাচ্ছে, তাই নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা দরকার। উপদেষ্টারা যদি এই মানসিকতায় চলে যান, তাহলে সরকারের মূল ‘বিপ্লবী স্পিরিট’ ধ্বংস হয়ে যাবে।”
অন্যদিকে, অধ্যাপক লুবনা আরেফিন বলেন,
“অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য নির্ভর করবে তাদের নৈতিক অবস্থান কতটা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার ওপর। যদি জনগণ মনে করে, তারাও আগের সরকারের মতো স্বার্থান্বেষী, তাহলে বিশ্বাস হারানো সময়ের ব্যাপার মাত্র।”
সায়ের আরও অভিযোগ করেছেন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এখনো এমন কর্মকর্তারা রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা বা অনিয়মের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা প্রভাবশালী পদে বহাল আছেন।
তার ভাষায়,
“এভাবে যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হয়, তাহলে জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।”
তার এই বক্তব্য অনেকের কাছে প্রতিধ্বনির মতো শোনাচ্ছে—যেন জনগণ যা বলতে চাচ্ছে, সেটিই তিনি তুলে ধরেছেন।
সামাজিক মাধ্যমে ‘সেফ এক্সিট’ হ্যাশট্যাগে হাজারো মন্তব্যে ভরে গেছে।
অনেকে লিখেছেন—
“যে বিপ্লবের নামে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, সেটি এখন ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার মঞ্চে পরিণত হচ্ছে।”
আবার কেউ কেউ বলছেন,
“জুলকারনাইন সাহস করে মুখ খুলেছেন, কিন্তু তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারলে এটি হবে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বড় ধাক্কা।”
অভ্যন্তরীণ এই বিতর্ক এখন কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়— এটি সরকার পরিচালনার দিকনির্দেশনা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে বলে একাধিক সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে।
একজন ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেন,
“উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন ইতিমধ্যেই নিজেদের পদত্যাগের বিকল্প ভাবছেন। আবার কেউ কেউ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়ে যোগাযোগ রাখছেন।”
সামাজিক বিশ্লেষকরা বলছেন,
“যখন কোনো সরকার নৈতিকতার পতাকা উঁচিয়ে ক্ষমতায় আসে, তখন তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড জনমনে মূল্যায়িত হয় দ্বিগুণভাবে। যদি সেখানে সামান্য অনিয়মও প্রকাশ পায়, তা আস্থা ভাঙার জন্য যথেষ্ট।”
একজন নাগরিক সংগঠনের নেতা বলেন,
“এই সরকার যদি সত্যিই জনগণের সরকারের প্রতিশ্রুতি রাখতে চায়, তাহলে তাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত এই অভিযোগগুলো তদন্তে আনা এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা করা।”
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এমন সংবেদনশীল সময়ের মধ্যে যদি সরকারের ভেতরে বিভাজন বাড়ে, তাহলে আন্তর্জাতিক অংশীদাররাও সতর্ক হয়ে উঠবে।
বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগ, উন্নয়ন প্রকল্প ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ বলেন,
“যদি সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেই অবিশ্বাস ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে বিদেশি সহযোগী রাষ্ট্রগুলো আস্থা হারাবে।”
দেশের সাধারণ মানুষ এখন চায়— এই সরকার তার প্রতিশ্রুত পরিবর্তন বাস্তবে প্রমাণ করুক।
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্বই হতে পারে তার মূল ভিত্তি।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন,
“সায়েরের মতো অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বক্তব্য উপেক্ষা না করে বরং সেগুলো যাচাই করা সরকারের দায়িত্ব। নইলে এই বিতর্ক ভবিষ্যতে আরও বড় রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিতে পারে।”
জুলকারনাইন সায়েরের “সেফ এক্সিট” প্রসঙ্গে দেওয়া মন্তব্য যেন এক অজানা দরজা খুলে দিয়েছে।
এর ভেতরে লুকিয়ে আছে ক্ষমতার জটিলতা, নৈতিকতার সংকট ও নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা।
যদি তার অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে এটি শুধু একজন উপদেষ্টার নয়— পুরো সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর প্রশ্ন তুলে দেবে।
আর যদি মিথ্যা হয়, তাহলে সরকারের উচিত দ্রুত তদন্ত করে সত্য উদঘাটন করা, যাতে জনগণের আস্থা ফিরে আসে।
অবশেষে, প্রশ্ন একটাই—
এই অন্তর্বর্তী সরকার কি সত্যিই “বিপ্লবের স্পিরিট” রক্ষা করতে পারবে, নাকি ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়ে পরিণত হবে কেবল আরেকটি ব্যর্থ প্রতিশ্রুতিতে?