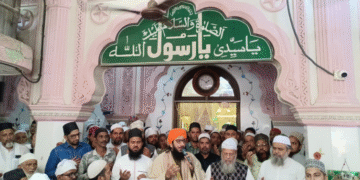আকারভিত্তিক সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব
বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ শুধু স্বাদের জন্য নয়, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতিবছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে ইলিশের মৌসুম ঘিরে নদী, ঘাট ও বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই আনন্দে ভাটা পড়ছে মূলত ইলিশের লাগামহীন দাম বৃদ্ধির কারণে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। চলতি মৌসুমে ইলিশের দাম প্রতি কেজিতে ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।
এমন অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে ইলিশের আকারভিত্তিক সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে দাম বাড়ার পেছনে ১১টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলো সমাধানে নীতি-পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে দেশের বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা বাজারে ইলিশের দাম ওঠানামা করেছে ৯০০ থেকে ২২০০ টাকার মধ্যে। বাজারের বাস্তব চিত্র হলো—ছোট আকারের ইলিশের দাম যেখানে ৯০০ টাকা, সেখানে বড় আকারের মানসম্পন্ন ইলিশের দাম প্রতি কেজি ২০০০ টাকারও বেশি। এই পরিস্থিতি সাধারণ ভোক্তাদের জন্য চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।
বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, জুন মাসে ইলিশের দাম ছিল ৬০০ থেকে ২২০০ টাকা। জুলাই মাসে দাম বেড়ে হয় ৯০০ থেকে ২০০০ টাকা। আগস্টে সরবরাহ কিছুটা বেড়ে দাম নেমে আসে ৮০০ থেকে ২০০০ টাকায়। কিন্তু সেপ্টেম্বরে আবার বেড়ে তা দাঁড়ায় ৯০০ থেকে ২২০০ টাকায়।
অন্যদিকে, একই সময় ভারতে রপ্তানি করা ইলিশের গড় দাম পড়ছে প্রতি কেজি মাত্র ১৫৩৪ টাকা। অর্থাৎ স্থানীয় বাজারে ভোক্তারা যে দাম দিচ্ছেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাজারদরের তুলনায় বেশি। এতে বোঝা যায়, ভোক্তাদের ওপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।
বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান জানিয়েছেন, সরেজমিন সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়েছে—ইলিশ মাছ শতভাগ দেশীয় পণ্য হলেও বাজারে এর দামের সঙ্গে কৃত্রিমতা জড়িয়ে আছে। কারণ, ইলিশ আহরণ বা উৎপাদনে আন্তর্জাতিক বাজার কিংবা ডলারের ওঠানামার প্রভাব খুবই সীমিত। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে আহরণের পর বাজারে প্রবেশের বিভিন্ন স্তরে অস্বচ্ছতা।
মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ, দাদন ব্যবসায়ীদের কারসাজি এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার কারণে ইলিশের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃত জেলে বা প্রান্তিক বিক্রেতারা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, বরং মুনাফা যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের হাতে।
প্রতিবেদনে ইলিশের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ১১টি কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো—
- চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যহীনতা
- মজুতদারি ও সিন্ডিকেটের প্রভাব
- জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি
- পরিবহন খরচ বৃদ্ধি
- নদীর নাব্যতা সংকট ও পরিবেশগত সমস্যা
- অবৈধ জালের ব্যবহার
- দাদন ব্যবসার দৌরাত্ম্য
- বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব
- নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা
- মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ
- রপ্তানির চাপ
এগুলো একসঙ্গে কাজ করে বাজারে অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য ইলিশ কেনা কঠিন করে তুলছে।
বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য বিটিটিসি সুপারিশ করেছে—ইলিশের আকার অনুসারে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হোক। যেমন ছোট, মাঝারি ও বড় সাইজের ইলিশের জন্য আলাদা আলাদা মূল্যসীমা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। এতে একদিকে ভোক্তা নির্ধারিত দামে মাছ পাবেন, অন্যদিকে প্রান্তিক বিক্রেতারাও ন্যায্য দাম নিশ্চিত করবেন।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ব্যবস্থা শুধু ইলিশ নয়, ডিম, মুরগি ও ভোজ্যতেলসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রেও কার্যকর হতে পারে।
গত পাঁচ বছরে স্থানীয় বাজারে ইলিশের দাম বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। একই সময়ে রপ্তানি মূল্যও বেড়েছে, তবে স্থানীয় বাজারের তুলনায় রপ্তানি দাম অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ, সেপ্টেম্বরে ভারতে রপ্তানি হওয়া ইলিশের গড় মূল্য ছিল ১৫৩৪ টাকা, যেখানে স্থানীয় বাজারে সর্বোচ্চ দাম উঠেছে ২২০০ টাকা।
এই বৈপরীত্যের ফলে একদিকে দেশীয় ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে বিদেশি ক্রেতারা তুলনামূলক সস্তায় ইলিশ পাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ন্যায্য মূল্যনীতি প্রণয়ন না করলে এই অসামঞ্জস্য দীর্ঘমেয়াদে জেলেদের জীবনমান ও ভোক্তা স্বার্থ উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
দাদন ব্যবসায়ীদের ভূমিকা
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইলিশের দামের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে দাদন ব্যবসায়ী চক্র। এরা মূলত জেলেদের আগাম অর্থ দিয়ে মাছ কেনার অধিকার নিশ্চিত করে নেয়। পরে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ইলিশের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে ভোক্তারা অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হন এবং প্রকৃত জেলেরা বঞ্চিত হন ন্যায্য মুনাফা থেকে।
ইলিশের উৎপাদন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ নদীর নাব্যতা সংকট ও দূষণ। বিভিন্ন এলাকায় নদী খনন না হওয়া, পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি এবং শিল্পবর্জ্য মিশে ইলিশের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়ছে। একইসঙ্গে অবৈধ জাল ব্যবহার ইলিশের প্রজনন ও টিকে থাকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
বাজার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশগুলো হলো—
- আকারভিত্তিক সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ
- দাদন ব্যবসায়ী ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ
- মধ্যস্বত্বভোগীর স্তর কমানো
- প্রান্তিক বিক্রেতাদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা
- পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ ও নদী খনন
- অবৈধ জাল বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা
- ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় বাজার তদারকি জোরদার করা
ইলিশ শুধু একটি মাছ নয়, এটি বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়ের অংশ। কিন্তু অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সিন্ডিকেটের কারসাজি এবং রপ্তানির বৈপরীত্যের কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রস্তাবিত আকারভিত্তিক খুচরা মূল্য নির্ধারণ যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বাজারে স্বস্তি আসবে, ভোক্তারা ন্যায্য দামে ইলিশ পাবেন এবং প্রান্তিক জেলেরা তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পাবে।
সার্বিকভাবে, ইলিশের বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে কেবল অর্থনীতিই নয়, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিও সমুন্নত থাকবে।